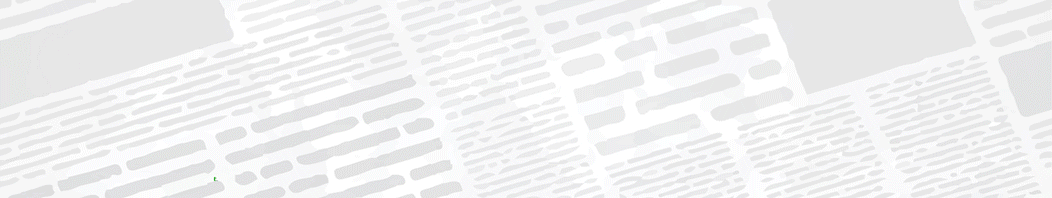
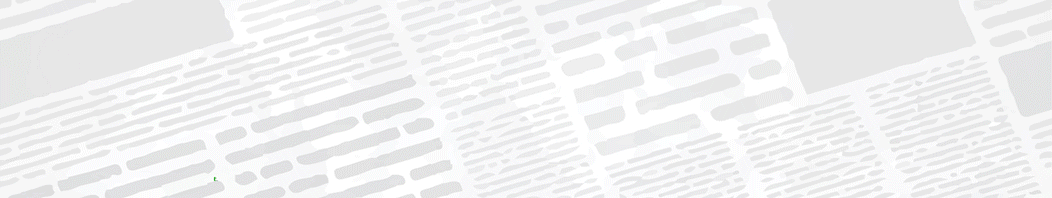
০৯ ডিসেম্বর, ২০২২
 জুয়েল রানা,
জুয়েল রানা, 


ছবি: বেগম রোকেয়া।
মহানবীর মাধ্যমে আল্লাহর প্রথম বাণী ছিল, ‘পড়ো’ অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করো। সে জন্যই মহানবী বলেছেন, শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের জন্যই ফরজ। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোনো প্রভেদ নেই। বরং নারী বিনে পুরুষ অসমাপ্ত, আবার পুরুষ ছাড়া নারী অসম্পূর্ণ। সৃষ্টিকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই নারীর সৃষ্টি। আর এই সৃষ্টিকে সার্থক করতে, সফল করতে, সুন্দর করতে পুরুষের যেমন শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনই নারীর শিক্ষাও অপরিহার্য। তবু এ কথা সত্য যে নারীশিক্ষার বিষয়টি বিভিন্ন সময়ে চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে, অবহেলিত হয়েছে। নারী প্রগতির দিশারী। বেগম রোকেয়া দুঃখ করে বলেছিলেন, ‘স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করিতে ব্যস্ত, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ-প্রস্থ মাপেন, সেলাই করিবার জন্য।’
ধর্মীয় গোঁড়ামি আর সংকীর্ণতার কারণে অতীতে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটানোর রীতি এ দেশে ছিল না বললেই চলে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কয়েকজন উদার চিন্তার প্রগতিশীল মানুষের প্রচেষ্টার ফলেই এ দেশে নারীশিক্ষার সূচনা হয়। সর্বপ্রথম শ্রীরামপুরে মিশনারিরাই নারীশিক্ষার উদ্যোগ নেন। ১৮১১ সালে ৪০টি বালিকা নিয়ে উইলিয়াম কেরি-মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ধর্ম শিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলেন। ১৮১৮ সালে চুচুরায় বালিকাদের জন্য আলাদা একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লন্ডন মিশনারি সোসাইটির রবার্ট মের প্রচেষ্টায়। এরপর ১৮১৯ সালের মে-জুনে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের স্ত্রীদের উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলার কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘দি ফিমেল জুভেনাইল’ নামে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের প্রতিষ্ঠান। এ সময় রাধাকান্ত দেব ও গৌরীমোহন বিদ্যালংকার বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হন। এইভাবে খুব ধীরগতিতে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর প্রচেষ্টা চলতে থাকলেও তখনো সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া দোষের বলে গণ্য হতো। মেয়েদের জন্মের পর থেকে তাদের অবরুদ্ধ করে রাখা হতো, নানা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক বিধিনিষেধে মেয়েদের মধ্যে ভয়ভীতি জাগিয়ে রাখা হতো।
মিশনারিদের উদ্যোগের ফলে নারীশিক্ষার প্রতি এ দেশের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ে। মেরি অ্যান কলকাতায় এসে চার্চ মিশনারি সোসাইটিতে যোগ দেন এবং কিছুদিনের মধ্যে কলকাতার কুমারটুলী, মল্লিকবাজার, শ্যামবাজার, ঠনঠনিয়া, মির্জাপুর ইত্যাদি স্থানে মেয়েদের জন্য আটটি স্কুল শুরু করেন। ১৮২৪ সালের মধ্যে মেয়েদের জন্য ২৪টি স্কুল খোলা হয়। মিশনারিদের পরিচালনায় যখন ৩০টি স্কুল চালু ছিল, তখন দেশীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগে আরও কয়েকটি স্কুল খোলা হয়। রাজা রামমোহন রায় নারীশিক্ষার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। এ ছাড়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ও ব্রাহ্ম-সমাজের মাধ্যমে নারীশিক্ষার সমর্থনে বক্তব্য প্রচার করতে থাকেন।
তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর এবং শিক্ষা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট জন এলিয়ট ডিংকওয়াটার বেথুন ১৮৪৯ সালের ৭ মে কলকাতায় ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’ নামে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই নারীশিক্ষা নিকেতনটি পরবর্তীকালে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় নামে খ্যাতি লাভ করে। পরে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের অনুসরণে আরও স্কুল খোলা হয়। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়টি ১৮৭৯ সালে বেথুন মহিলা কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং এটিই ছিল ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা কলেজ। নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে থাকা বঙ্গনারী-সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজেও ১৮৫৭-৫৮ সালে বাংলায় বিভিন্ন জেলায় মেয়েদের জন্য ৩৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এসব স্কুলে প্রায় ১ হাজার ৩০০ ছাত্রী পড়ত।
১৮৬৩-৬৪ সালে ঢাকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল ও সাধারণ স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ১৬। তবে সে সময়ে শিক্ষিকার অভাব নারীশিক্ষা প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৬৭-৬৮ সালে পূর্ববঙ্গের ছয়টি স্কুলে মাত্র ছয়জন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথার জন্যই মেয়েদের শিক্ষার চরম এই দুরবস্থা ছিল।
বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের গোঁড়ামির কারণে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তখনো কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় মুসলিম সমাজের অবরোধ প্রথার কঠোর শৃঙ্খলা ভেঙে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পরবর্তী পাঁচ দশকের মধ্যে যে কয়েকজন মহীয়সী নারীশিক্ষার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বিবি তাহেরুননেছা, কুমিল্লার নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩) এবং রংপুরের কুরিমুন্নেসা খানমের (১৮৫৫-১৯২৬, বেগম রোকেয়ার বড় বোন) নাম উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া ওই সময়ে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য আরও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন মুর্শিদাবাদের নওয়াব ফেরদৌস মহল এবং খুজিস্তা আক্তার বানু (হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাতা)।
এই সময়েই মুসলিম নারীশিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের আবির্ভাব মুসলিম নারী সমাজের জন্য ছিল আশীর্বাদস্বরূপ। তার প্রতিভা আর মহৎ উদ্যোগ সেকালের ভগ্নহৃদয় মুসলমান সমাজের জন্য এক দৈব আশ্বাস। তার মতো বুদ্ধিদীপ্ত, আত্মনির্ভরশীল ও দৃঢ়প্রত্যয়ী শিক্ষানুরাগীর জন্ম মুসলিম নারী সমাজে নবজাগরণের সৃষ্টি করে। সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামের রক্ষণশীল মুসলিম জমিদার বংশে জন্ম নেন। তিনি ১৮৯৭ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামীর উৎসাহে তিনি বাংলা-ইংরেজি শেখেন। ১৯০৯ সালে তার স্বামী মারা যান। বিধবা হওয়ার পাঁচ মাস পর মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য ব্রতী হয়ে মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে একটি স্কুল চালু করেন। তারপর ১৯১০ সালে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতায় তালতলা ওলিউল্লা লেনে মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে মরহুম স্বামীর নামানুসারে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেটিই অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম মেয়েদের জন্য প্রথম স্থায়ী স্কুল। রোকেয়াকে এ কাজে সহযোগিতা করেছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকসহ সেই সময়ের শিক্ষিত বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিরা।
অনেক প্রচেষ্টার পর ১৯১৭-তে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটি মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুলে এবং ১৯৩১-এ উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষয়ত্রী ও সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করে বেগম রোকেয়া কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। স্কুলের উন্নতির জন্য নিজের অর্থ ব্যয় করতেন। মুসলিম নারীশিক্ষার অন্ধকার যুগে কলকাতার বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। সেই কুসংস্কারের যুগে নানা প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সত্ত্বেও বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষা প্রসারের কর্তব্য কর্ম থেকে সামান্যও বিচ্যুত হননি। বলা যায়, নারীশিক্ষার উন্নয়নের জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন।
ক্রমান্বয়ে উদার ও প্রগতিশীল চিন্তার উন্মেষ ঘটতে শুরু হলো। নারীশিক্ষার রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেল এবং নারীশিক্ষার প্রসার হতে লাগল। সমাজের অনেকেই বুঝতে শিখলেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যই শিক্ষা অপরিহার্য। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। এ জন্য বেগম রোকেয়া নারী সমাজের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার লক্ষ্যে নারীশিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে সারা জীবন কাজ করেছেন, সংগ্রাম করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। সব কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে তাদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে হবে।
বেগম রোকেয়া দ্বার্থহীনভাবে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেছেন, কন্যাসন্তানদের অলংকার দিয়ে না সাজিয়ে বরং সেই অর্থ দিয়ে মেয়েদের শিক্ষার আলো দিতে হবে। মেয়েরা পুরুষের সমান মর্যাদা নিয়ে জন্মায়, কিন্তু শিক্ষার অভাবেই তারা প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই মেয়েদের শিক্ষিত করতে হবে, তবেই তাদের পরনির্ভরশীলতা দূর হবে এবং সমাজ উন্নয়নে ও জাতি গঠনের কাজে পুরুষের পাশে তারা সমানভাবে অংশ নিতে পারবে। তাই আর করুণা নয়, বরং অধিকার ও মর্যাদা দিয়েই তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত বেগম রোকেয়া সারা জীবন নিরলস সংগ্রাম করে ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। চরম প্রতিকূলতার মাঝেও এ দেশের মুসলিম নারীশিক্ষার উন্নয়নের ইতিহাসে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।
পরিশেষে বলতে হয়, ছেলে-মেয়ে উভয়েই আল্লাহর সৃষ্টি। তাই একজনকে অন্যজনের ওপর প্রাধান্য দেয়ার কোনো কারণ নেই। কন্যা ও পুত্র উভয়ই সন্তান হিসেবে স্বীকৃত, বিধায় উভয়ের প্রতি একই প্রকার আচরণ করতে হবে। কোনো পিতা-মাতাই যেন পক্ষপাতিত্ব করে পুত্রসন্তানকে প্রাধান্য দিয়ে কন্যাসন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না করেন। বরং শিক্ষার আলোতেই নারী ও পুরুষের বৈষম্যের অবসান হবে, এই প্রত্যাশাই করি।
লেখক: অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ : মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান